আল বেরুনির “ভারত তত্ত্ব” - ফেরদৌস আহমেদ
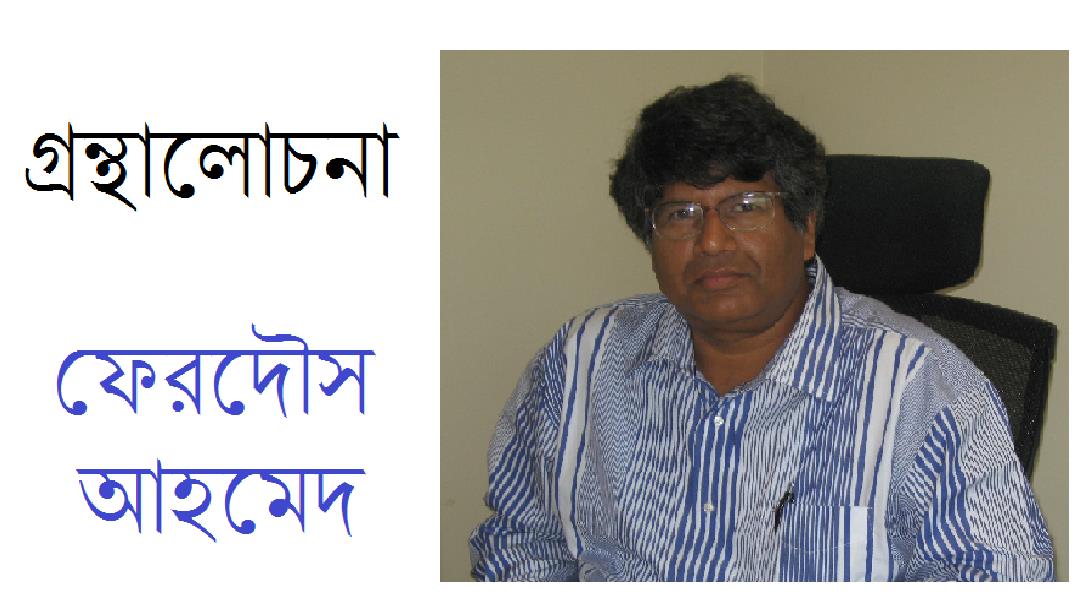
আল বেরুনির “ভারত তত্ত্ব” বইটির বাংলা অনুবাদ সম্প্রতি পড়লাম। আল বেরুনির আসল নাম আবু রায়হান মুহম্মদ বিন আহমদ; আল বেরুনি (অর্থ বাহিরাগত) তাঁর উপাধি। বইটির আসল নামও লম্বা চওড়া – “হিন্দুদের সব রকম চিন্তা পদ্ধাতির সঠিক বর্ণনা, বুদ্ধি বিচারে যা গ্রহনযোগ্য আর যা গ্রহনযোগ্য নয়”। মূল আরবি (১০৩১ সালে লিখিত) থেকে বাংলা অনুবাদ করেছেন সুপণ্ডিত জনাব আবু মহামেদ হবিবুল্লাহ। ১৯৭৪ সালে বাংলা একাডেমী এটি প্রাকাশ করলেও এতদিন নজরে পরে নি; এবার ঢাকা যেয়ে দিব্য প্রকাশের ২০০৬ মুদ্রনটি চোখে পড়ল।
হাজার বছর পুরানো হওয়া সত্তেও – কিংবা হয়তো সেকারণেই – বইটি খুব তথ্যবহুল, শিক্ষামূলক এবং উপভোগ্য। আমি সবাইকেই এই বইটি পড়তে উৎসাহিত করি। আমি নিজে বইটি পড়ে অনেক কিছু শিখেছি, অনেক কিছু বুঝেছি। ভাবলাম ব্যাক্তিগত ভাবে যে বিষয় গুলো আমার কাছে ভাল লেগেছে বা গুরুত্বপূর্ণ মনে হয়েছে সেগুলো নিয়ে একটু আলোচনা করি।
বইটির গোড়াতেই আল বেরুনি লেখকের সততার এবং সাহসের উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। সত্য উদ্ঘাটন এবং প্রকাশের জন্য মৃত্যুকে অবজ্ঞা করতে বলেছেন। কথাটি চির সত্য – তখন তো বটেই, এখন আরো বেশি। কিন্তু ভারতবর্ষ সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ সে যুগে সহজ ছিল না। লিখিত প্রায় সব কিছুই ছিল ‘নকলের নকল’। ভারতীয় লিপিকাররা খুব অসাবধান ছিলেন। যার ফলে অনেক পাণ্ডুলিপিই ছিল ভুলে ভরা। তাছাড়া আল বেরুনির পর্যবেক্ষণ অনুসারে সে যুগে ভারতীয়দের স্বভাব ছিল জ্ঞান বিতরণে কার্পণ্য করা। তারা বিদেশীদের এবং বিদেশ ভ্রমণ এড়িয়ে চলত। অন্ধ অনুসরন ও পুনরাবৃত্তি ছিল লেখক-পণ্ডিতদের স্বভাব।
ঈশ্বর সম্বন্ধে হিন্দুদের বিশ্বাস ছিল এই যে তিনি এক, চিরন্তন, অনাদি, অনন্ত, স্বাধীন, সর্বশক্তিমান, সমস্ত জ্ঞানের আকর, চিরঞ্জীব, প্রানদাতা, সর্বনিয়ন্তা ও সৃষ্টিপালক। তিনি সমস্ত সাদৃশ্য বা বৈপরীত্যের অতীত; তাঁর শক্তির তুলনা তিনিই; কিছুই তাঁর মতো নয়, তিনিও কোনকিছুর মতো নন। এই বিশ্বাস মুসলমানদের একেশ্বরবাদের খুব কাছাকাছি। এবং সাধারণ ভাবে প্রচলিত হিন্দু পৌত্তোলিকতা থেকে বেশ দূরে। হিন্দুরা এও মনে করত যে সমস্ত বস্তুই ঈশ্বরের অংশ। আল বেরুনি লক্ষ করেছিলেন যে সাধারণ মানুষই মূর্তি পূজা করে; কিন্তু যারা ধর্ম ও দর্শনের আসল অর্থ বোঝে তারা ঈশ্বর ছাড়া অন্য কাউকে উপাসনা করে না।
বিষ্ণুপুরাণে বলা হয়েছে পদার্থ হচ্ছে জগতের মূল সত্তা। পৃথিবীতে যা কিছু ঘটে তা পদার্থের নিজেস্ব স্বভাবের দরুন। সমস্ত কর্মই জড় পদার্থ থেকে উদ্ভুত। বহু যুগের বহু দার্শনিক ও বিজ্ঞানী এই বস্তুতান্ত্রিক মতে বিশ্বাসী। সে হিসাবে বিষ্ণুপুরাণের এই মত সার্বজনীন। হিন্দুরা আরও মনে করত পদার্থ সব সময়ই শ্রেয় থেকে শ্রেয়তরের দিকে যায়; অর্থাৎ শক্তি থেকে ক্রিয়ার দিকে যায়। পৃথিবীতে সব ক্রিয়াই পদার্থের নিজেস্ব স্বভাবের পরিণতি। পদার্থ থেকেই কর্মের উৎপত্তি। আধুনিক বিজ্ঞান ‘পদার্থ থেকেই কর্মের উৎপত্তি’ এটা না বললেও স্বীকার করে যে বিশ্বে সময়ের সাথে বিশৃংখলা (এনট্রপি) বাড়ছে। এর মানে ‘পদার্থ শ্রেয় থেকে শ্রেয়তরের দিকে যাচ্ছে তা নয়, যদি না আমরা বিশৃংখলাকে একটা ভাল জিনিষ মনে করি।
পাতঞ্জল গ্রন্থে বলা হয়েছে যে অজ্ঞান-ই আত্মার শৃঙ্খল। তাই জ্ঞান অর্জনের দরকার। বাসুদেব বলেছেন “প্রজ্ঞা যার লাভ হয়েছে সেই শ্রেষ্ঠ মানুষ, কারন সে ঈশ্বরানুরক্ত এবং ঈশ্বরও তাঁর অনুরাগী”। ইসলামের সাথে মিল এখানে সহজেই চোখে পড়ে। ইসলাম বলে জ্ঞানের জন্য সুদূর চীনে যাও; মুর্খের উপাসনার চেয়ে জ্ঞানীর নিদ্রা শ্রেয়। গীতাতে বলা হয়েছে জ্ঞান সঞ্চয় করার জন্যই মানুষের সৃষ্টি। হিন্দুদের মতে মানুষের মন ও ইন্দ্রিয় জ্ঞান সঞ্চয়ের জন্য সৃষ্টি হয়েছে। বুদ্ধির নিকটতম সহকারী হচ্ছে চিন্তা (বা ধ্যান) এবং দূরতম সহকর্মী হচ্ছে পঞ্চেন্দ্রিয়। জ্ঞানের পবিত্রতা অন্য সব বস্তুর পবিত্রতা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। জ্ঞানের জন্যেই ঋষিরা মানুষ হয়েও দেবতাদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ। জ্ঞান মার্গে যে মোক্ষ লাভ হয় তা আবার পাপ পরিহার না করলে হয় না। এ পাপের নানা শাখা-প্রশাখার মধ্যে লোভ, ক্রোধ ও মূর্খতা অন্যতম। স্পষ্টতই বোঝা যাচ্ছে মোক্ষ লাভ খুব কম লোকের ভাগ্যেই আছে।
অন্তত আমার ভাগ্যে নেই। সে যাই হোক, জ্ঞান অর্জনের মাধ্যমে মোক্ষ লাভ না হয় নাই হলো। কিন্তু মোক্ষ লাভের আরেকটি উপায় গীতাতে আছে যেটা আমার মনে ধরেছে, এবং বলা চলে বাল্য কাল থেকেই এটা আমি পালন করে আসছি। সেটা হোল কর্তব্যাকর্তব্যের বিষয়ে মানুষ ভ্রমে পতিত হয়। কর্মের ভালমন্দ নির্ণয় করার কোনো আদর্শ তার নেই। কাজেই কর্ম ত্যাগ করা এবং কর্মের সাথে অসম্পৃক্ত থাকাই প্রকৃত কর্ম। আমাদের মতো অলসদের জন্য এটা ঈশ্বর প্রদত্ত।
অন্যান্য ধর্মের মতো হিন্দু ধর্মেও বলা হয়েছেঃ মিথ্যা বলো না, খুন করো না, উপাসনা করো, ইত্যাদি, ইত্যাদি সব ভাল কথা। এসব গতানুগতিক উপদেশ ছাড়াও কিছু মজার কথা আছে। যেমন ধন সঞ্চয় করো না। পার্থিব সম্পদের হীন দাসত্ব থেকে মুক্তি লাভ করে মানুষ পরম শান্তি পেতে পারে। অন্ন, বস্ত্র ও আশ্রয়ের প্রয়োজন থেকে মানুষের মুক্তি নাই; তাই এসবের জন্য কোন ক্ষতি হয় না। কিন্তু অন্নবস্ত্রের অতিরিক্ত যা কিছুর অভাব মানুষ বোধ করে, আপাতত সুখদায়ক হলেও আসলে তা কষ্টের ছদ্মরুপ; তাতে নিমগ্ন থাকা সর্বনাশকর, কঠিনতম যন্ত্রণা যার পরিণাম। গ্রীক দার্শনিক সক্রেটিশও বলেছিলেন আমি যে সৎ জীবন যাপন করেছি তার প্রমাণ আমার কোন ধনদৌলত নেই। হু, ভাবছি এখনকার দিনে মানুষ কি ভাবে; থাক, জিজ্ঞেস না করাই ভাল।
স্বর্গ ও নরকের বহুল বর্ণনা হিন্দু শাস্ত্রে আছে। বিষ্ণুপুরাণ মতে আশি হাজার নরক আছে। প্রত্যেক পাপের জন্যে পৃথক নরকের ব্যাবস্থা আছে। সুক্ষাতিসুক্ষ বিচারের ব্যাপক আয়োজন। প্রাচলিত পাপ ছাড়াও কয়েকটি অসাধারণ পাপের উল্লেখ আছে। যেমন, তরবারি নির্মাতারা ‘বিযাসন’ নরকে যাবে; বৃক্ষ কর্তনকারীরা ‘অসিপত্রবন’ নরকে যাবে। এ থেকে ধারনা করা যায় যে হিন্দু মনিষীরা যুদ্ধ অপছন্দ করতেন এবং পরিবেশ রক্ষায় সচেতন ছিলেন। রাজার প্রাপ্য না দেয়ার উদ্দেশে যে ধন গোপন করে সে ‘অধোমুখ’ নরকে যাবে। যে কোন দেশের কর বিভাগ এটি শুনলে উদ্বাহু নৃত্য করবে।
হিন্দুদের বর্ণ প্রথার কথা সবাই জানে এবং আজ কালকার দিনে সবাই এটার নিন্দা করে। কিন্তু প্রাচীন কালের অনেক সমাজেই এ ধরনের প্রথা ছিল; যেমন ইরানে। গ্রীক দার্শনিক প্লেটোর ‘রিপাবলিক’ গ্রন্থেও জনসাধারণকে বিভিন্ন গোত্রে বিভক্ত করা হয়েছে। হিন্দু সমাজ সে সময়ে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এ চার বর্ণে বিভাক্ত ছিল; এখনও আছে। সমাজে তাদের স্থান, পেশা, কর্তব্য ও চলনবিধি সবই নির্দিষ্ট করা; কেও তার বাইরে যেতে পারে না। ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় ছাড়া কেও মোক্ষলাভ করতে পারে না, কারণ তাদের বেদাধ্যয়নের অধিকার নেই। কিন্তু ধর্মের এ বিধান পরবর্তী যুগের অনেক পণ্ডিত মেনে নিতে পারেন নি। ব্যাস বলেছিলেন পূর্ণ জ্ঞান লাভ করার পর একজন মানুষ যে কোন ধর্মই গ্রহন করুক না কেন তার মুক্তি হবেই। বাসুদেবের মতে কর্মের প্রতিদানে ঈশ্বর পক্ষপাত করেন না। মুক্ত বুদ্ধির পণ্ডিতগণ যে কোন ধর্ম বা মতবাদ বিনা বিচারে মেনে নেন না এটা তার নিদর্শন। প্রয়োজনে তাঁরা নিজের মতামত ব্যাক্ত করেন (অনেক ক্ষেত্রেই জান-মালের ঝুকি নিয়ে)।
আল বেরুনি বেদ-বেদান্ত পুরাণ ইত্যাদি ধর্ম গ্রন্থের বিশদ বর্ণনা দিয়েছেন। মহা ভারতের এক অংশ ব্যাস নামক এত ব্রাহ্মণ লিখেছিলেন। তিনি তার লিপিকার নিনায়ককে নির্দেশ দিয়েছিলেন সে যেন অর্থ না বুঝে কোন বাক্য না লিখে। এই জ্ঞানগর্ভ উপদেশ আল বেরুনির মনে দাগ কেটেছিল।
হিন্দুদের ব্যাকরণ ও ছন্দ শাস্ত্রের বিষদ আলোচনা আল বেরুনি করেছেন। তিনি ‘ইউক্লিড’, ‘আলমাগেস্ট’ ইত্যাদি বিখ্যাত বইয়ের সংস্কৃত তর্জমাও করেছিলেন। হিন্দুদের বাইশটি গ্রন্থও আল বেরুনি আরবীতে অনুবাদ করেছিলেন। সুতরাং জ্ঞান নেয়া দেয়া দুটোই এক সাথে হচ্ছিলো। বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় হিন্দুদের অবদানের ও বহু সংখ্যক পুস্তকের প্রসংশা আল বেরুনি করেছেন। ‘পঞ্চতন্ত্র’ তিনি তর্জমা করতে চেয়েছিলেন যদিও সেটা সম্ভব হয় নাই। ভারতীয়দের গণনা পদ্ধতি, পরিমানবিজ্ঞান, ভূগোল, রসায়ন বিদ্যা, গ্রহ নক্ষত্রের গতি বিধি, জোয়ার ভাটা, ইত্যাদি নানা বিষয়ের বিস্তারিত আলোচনা আল বেরুনি করেছেন।
হিন্দু মতে কলিযুগে পাপ বেড়ে যাবে এবং পুন্য একেবারে লোপ পাবে। সেই হচ্ছে মর্তবাসীদের ধ্বংস হবার সময়। রাজারা অত্যাচার, লুন্ঠন, উৎপীড়ন ও ধ্বংসে মেতে উঠবে। পণ্ডিতরা আর জ্ঞান অর্জন করতে পারবে না; বরং তারা শুধু প্রতারণা করবে। কেউ দারিদ্র্য ও সংযম সাধন করলে আশ্চর্য্য জীব বলে লোক তাকে অবজ্ঞা করবে। ইসলামে কিয়ামতের বর্ননার সাথে এর মিল লক্ষণীয়।
আরও মিল আছে, যেমন সাধ্য মতো দান করা হিন্দু দের অবশ্যকর্তব্য। ধার দিয়ে সুদ নেয়াও নিষিদ্ধ। মদ্য পান শূদ্র ছাড়া সবার জন্যে নিষিদ্ধ। হিন্দুধর্ম উপবাস করাকে (এক দিন থেকে এক মাস পর্যন্ত) উৎসাহিত করে যদিও তা বাধ্যবাধকতাহীন বা স্বেচ্ছামূলক। একজন পুরষ চারটি পর্যন্ত বিয়ে করতে পারবে। চারটির বেশী স্ত্রী গ্রহণ নিষিদ্ধ তবে একটির মৃত্যু হলে আরেকটি বিয়ে করতে পারবে। কিন্তু স্বামীর মৃত্যু হলে স্ত্রী অন্য স্বামী গ্রহণ করতে পারবে না। তার জন্য শুধু দুটি পথ খোলা – আমরণ বিধবা থাকা অথবা আগুনে পুরে মরা (সতীদাহ?)। মতান্তরে স্ত্রী গ্রহনের সংখা বর্ণ অনুযায়ী নির্ধারিত ছিল। ব্রাহ্মণ চারটি স্ত্রী গ্রহণ করতে পারে, ক্ষত্রিয় তিনটি, বৈশ্য দুইটি, আর শূদ্র একটি।
আল বেরুনি মধ্য এশিয়ায় আমুদরিয়া নদীর তীরে অবস্থিত প্রাচীন খোরেজম রাজ্যের কাস নামক গ্রামে ৯৭৩ খ্রিস্টাব্দে জন্ম গ্রহণ করেন। পড়ে তিনি উরগেঞ্জ শহরে বসবাস শুরু করলে আর সব বহিরাগতদের মতো তাঁর নামের সাথেও ‘আল বেরুনি’ লাগিয়ে দেয়া হয়। মুসলমানদের অবস্থান তখন অনেক উন্নত; রাজনৈতিক ভাবে তো বটেই, জ্ঞান বিজ্ঞানেও। গজনীর পরক্রান্ত নরপতি সুলতান মাহমুদ খোরেজম দখল করার পর অনেক সামরিক বেসামরিক লোককে বন্দি করে ভারতে নিয়ে আসেন। আল বেরুনিও এভাবে ভারতে আসেন এবং বন্দি আবস্থায় পাঞ্জাব ও সিন্ধুর কয়েকটি শহরে থাকেন। বন্দি অবাস্থাতেই তিনি ভারতীয় ও সংস্কৃতি সভ্যতা সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করেন। ভারত তত্ত্ব বইটি এরই সার্থক পরিণতি। অজানা দেশের অজানা ভাষা শিখে অজানা সব জটিল বিষয়বস্তু নিয়ে এত প্রতিকূল অবস্থায় এমন জ্ঞানগর্ভ বই মানব সভ্যতার এই সুদীর্ঘ ইতিহাসে আর দ্বিতীয়টি লেখা হয় নাই।
এ বিশাল গ্রন্থের শেষে আল বেরুনি লিখেছেন “এই রচনাতে অজ্ঞতা বশত কোন অসত্য কথা যদি এসে গিয়ে থাকে, আল্লাহ যেন আমায় ক্ষমা করেন এই আমার প্রার্থনা”। নির্ভিক সত্যবাদিতা এবং নির্মোহ জ্ঞানচর্চার এমন নিদর্শন সত্যিই বিরল। মানুষ যে ঈশ্বরের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি এমন মহা মানবেরাই তার প্রমাণ। আর জনাব হবিবুল্লাহ এ গ্রন্থ আনুবাদ করে বাংলা ভাষা ও সংকৃতির বিশেষ উপকার করেছেন। বাংলা ভাষা অনেক দিক দিয়ে উন্নত হলেও অনুবাদ সাহিত্যে দুর্বল। হবিবুল্লাহ সাহেবের মতো পারদর্শী ও উন্নত রুচির আরও অনুবাদক আমাদের দরকার।
ফেরদৌস আহমেদ
অটোয়া, কানাডা
Fahmed34@hotmail.com
-
গ্রন্থালোচনা // ভ্রমণ
-
17-01-2018
-
-