ফেসবুক রায় দেওয়ার প্ল্যাটফর্ম নয় - রমেন দাশ গুপ্ত
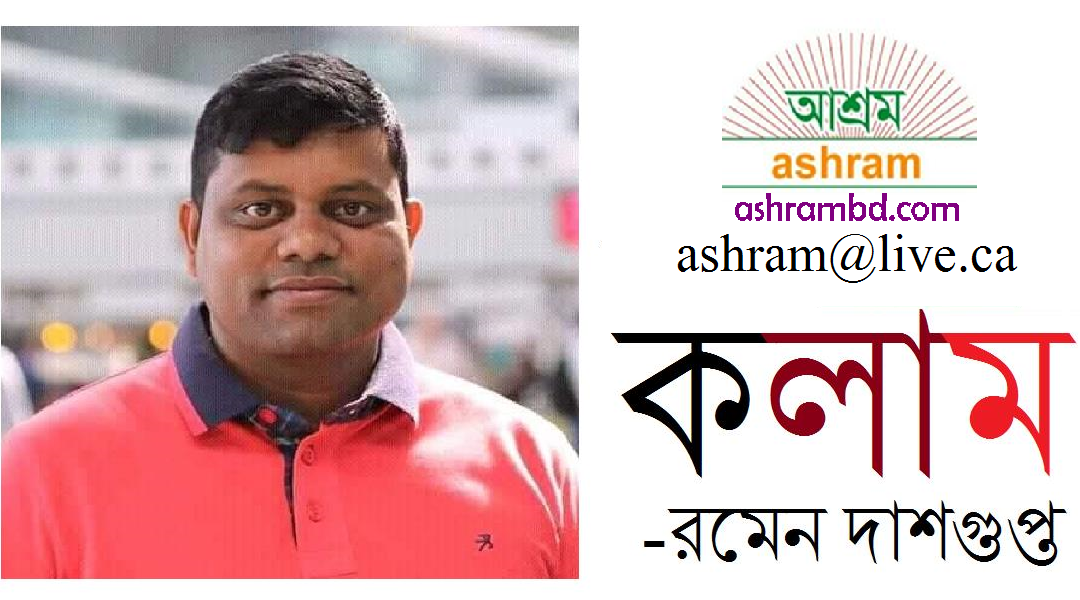
সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম হিসেবে ফেসবুক এখন বাংলাদেশে সবচেয়ে জনপ্রিয় নি:সন্দেহে। মানুষের প্রাত্যহিক জীবনে প্রয়োজনীয় উপাদানের মধ্যে এখন যেমন যুক্ত হয়েছে একটি মোবাইল ফোন, মোবাইল ছাড়া যেখানে মানুষের আর চলছেই না, তেমনই যেন ফেসবুকও। মোবাইল ব্যবহারকারী এবং ফেসবুক ব্যবহারকারীর সংখ্যার মধ্যে অবশ্যই অতিবিস্তর ফারাক আছে। ফেসবুকের তথ্য অনুযায়ী, বাংলাদেশে প্রায় আড়াই কোটি মানুষ ফেসবুক ব্যবহার করেন। বলা যেতে পারে, পৃথিবীর সমান্তরালে আরও এক পৃথিবীর বাসিন্দা বাংলাদেশের আড়াই কোটি ফেসবুক ব্যবহারকারী।
ফেসবুকের ব্যবহার বলতে, এই মাধ্যম ব্যবহার করে একে অপরের সঙ্গে যোগাযোগ করেন, তথ্য আদানপ্রদান হয়, ছবি-ভিডিও আপলোড করে বিনোদনে মেতে ওঠেন, লাইক-কমেন্ট-শেয়ার তো আছেই। এর বাইরেও ফেসবুকের নানাবিধ ব্যবহার আছে।
এর বাইরে যে বিষয়টির দিকে আলোকপাত করতে চাই, সেটি হচ্ছে- ফেসবুকে ব্যবহারকারীরা মতামত দেন, যুক্তিতর্কে মেতে ওঠেন। ক্ষুরধার, যুক্তিনির্ভর আলোচনার মাধ্যমে বিতর্কের দ্বার উন্মুক্ত করছে ফেসবুক, আবার নিজেরাই ফেসবুকে তার সমাধান খুঁজে নিচ্ছে। ২০১৩ সালে গণজাগরণ মঞ্চ থেকে শুরু করে বাংলাদেশে হাল আমলের অনেক জনপ্রিয় আন্দোলনেরও ভিত্তি বলা হচ্ছে ফেসবুককে। অসংখ্য ভালো কাজের মধ্যে ফেসবুক ব্যবহারকারীদের, যার মধ্যে আমি নিজেও একজন, আমি আমাদের মতামতগুলো নিয়ে আলোচনাটা এগিয়ে নিতে চাই।
প্রসঙ্গটা মতামত এবং যুক্তিতর্কের মধ্যে, আবারও বলছি ‘মতামত এবং যুক্তিতর্কের’ মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে পারলে ভালো লাগতো আলোচনায়। কিন্তু মতামত এবং যুক্তিতর্ক সবসময় নির্দিষ্ট পরিকাঠামোর মধ্যে থাকছে না, এমন অভিযোগ হরহামেশাই উঠছে এবং এই প্রেক্ষিতেই আলোচনার অবতারণা। মতামত অনেকসময় হয়ে উঠছে গুজব, আর ফেসবুক হয়ে উঠছে যুক্তিতর্ক ছাড়াই ধারণা ও আবেগের ভিত্তিতে রায় দেওয়ার প্ল্যাটফর্ম। মতামত অনেকসময় আরেকজনের চরিত্রহনন করছে, নিজের মতামতকে অন্যের উপর চাপিয়ে দেওয়ার মাধ্যম হিসেবেও তো ব্যবহার করা হচ্ছে ফেসবুককে।
সাম্প্রতিক সময়ের একটি ঘটনা বলি। শিক্ষামন্ত্রী ডা.দিপু মণির বরাত দিয়ে ফেসবুকে একটি মিথ্যা তথ্য ছড়িয়ে দেওয়া হয় যে, দেশের প্রতিটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থী ধর্মীয় আচার পালন বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। হঠাৎ ফেসবুকে ঝড়! সমালোচনার তীরে বিদ্ধ হতে লাগলেন শিক্ষামন্ত্রী। দেশের মূলধারার কোনো গণমাধ্যমে খবরটি নেই, অথচ সরব ফেসবুক ব্যবহারকারীরা। ‘এই তথ্য আপনারা কোথায় পেয়েছেন ? - ফেসবুকে পেয়েছি।’ হায়রে ফেসবুক ! পরে শিক্ষা উপমন্ত্রী মহিবুল হাসান চৌধুরী নওফেলকে এই বিতর্কের অবসান ঘটাতে ফেসবুকের দ্বারস্থ হতে হয়। উপমন্ত্রী জানান, এটি নিছক গুজব, মোটেও সত্যতা নেই।
২০১৮ সালে কোমলমতি শিক্ষার্থীদের আন্দোলনের সময় অভিনেত্রী নওশাবার ভিডিও বার্তাটির কথা একবার স্মরণ করুন। কি তুলকালাম কাণ্ডডই না ঘটিয়ে দিয়েছিল এই ভিডিওবার্তা! সেই আন্দোলনের সময় মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে উদ্ধৃত করে পর্যন্ত ফেসবুকে বিভ্রান্তিকর তথ্য প্রচার হয়েছিল। এগুলো একেবারে সাম্প্রতিক ঘটনা। এই ধরনের অসংখ্য ঘটনা আছে।
তবে আমার দৃষ্টিতে সবচেয়ে মারাত্মক হচ্ছে, কোনো স্পর্শকাতর ঘটনার পর মতামত দেওয়ার নামে আবেগপ্রবণ হয়ে রায় দিয়ে ফেলা। আমরা ফেসবুক ব্যবহারকারীরা সেক্ষেত্রে যুক্তিতর্কের বিষয়টাকে ধর্তব্য হিসেবে নেওয়ার প্রয়োজনই বোধ করি না। ঘটনার পেছনেও যে ঘটনা থাকে, সেই সত্যকে আমাদের আবেগপ্রবণ মন তুড়ি মেরে উড়িয়ে দেয়। বছর কয়েক আগে হোলি আর্টিজানে জঙ্গি হামলার ঘটনা কিংবা সাম্প্রতিক সময়ে নিজের ‘শিরায় বিষপ্রয়োগ করে এক চিকিৎসকের আত্মহত্যা’- কোনোটাতেই আমাদের আবেগপ্রবণ মন বাধা মানে না।
এই যে, যুক্তিতর্কের বাইরে গিয়ে আবেগপ্রবণ হয়ে মতামত দেওয়া, এতে কী হয় ? এতে তথ্যের সত্যতা খণ্ডিত আকার ধারণ করে, তথ্য বিকৃত হয়ে যায়। ঘটনা বিকৃতরূপ ধারণ করে, অনেকসময় প্রকৃত সত্য সামনে আসে না।
চট্টগ্রামের একজন জ্যেষ্ঠ্য আইনজীবী একবার ব্যক্তিগত আলাপচারিতায় বলেছিলেন, দেশে কোনো একটি অপরাধ সংঘটিত হলে, দায়ীদের দু’বার বিচার হয়। আদালতের আগেই গণমাধ্যম একবার বিচার করে ফেলে। অর্থাৎ গণমাধ্যম ঘটনার এত গভীরে চলে যায়, অনেকক্ষেত্রে আদালতে সেই সত্য প্রমাণ হয় না। প্রমাণ না হলে আসামি খালাস পায়। কিন্তু গণমাধ্যমের প্রচারের কাঠগড়ায় তো ততদিনে আসামি অনেকটাই দণ্ডিত হয়ে গেছেন।
এখন বলা হচ্ছে- কোনো অপরাধ কিংবা চাঞ্চল্যকর ঘটনার পর আসামিকে প্রথমে ফেসবুকের কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হয়, তারপর গণমাধ্যমের কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হয়, সবশেষে আদালতের কাঠগড়ায়। এখন তো আবার অনেকে ফেসবুককে বিকল্প গণমাধ্যম বলেও আখ্যায়িত করছেন। অথচ আমাদের ন্যায়বিচার পাবার জায়গা তো একটাই- আদালত।
‘শিরায় বিষপ্রয়োগ করে চিকিৎসকের আত্মহত্যা’র প্রসঙ্গটি আবার টেনে আনি। ওই চিকিৎসকের ভিডিওবার্তা থেকে যা জানা গেছে, তার স্ত্রীর একাধিক বিবাহবর্হিভূত সম্পর্ক ছিল। অস্বাভাবিক কিছু নয় এবং সমর্থনযোগ্যও নয়। পৃথিবী ছেড়ে যাওয়া চিকিৎসকের প্রতি ফেসবুকে সহানুভূতির ঝড়ও অস্বাভাবিক কিছু নয়। কিন্তু আমরা ফেসবুক ব্যবহারকারীরা একেকজন বিচারক সেজে বসে আছি। আমরা চিকিৎসকের স্ত্রীর জন্য ‘ক্রসফায়ার’ চাচ্ছি, প্রমাণের আগেই তাকে দণ্ড দিয়ে বসে আছি। এতে করে প্রমাণের আগেই মোটামুটি ফেসবুকে প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে যে, ওই নারী একজন খলনায়িকা (ক্ষমা প্রার্থনাপূর্বক)।
ঘটনার বিষয়ে আমরা ফেসবুক ব্যবহারকারীরাই যদি খণ্ডিত মানদণ্ড তৈরি করে দিই, তাহলে আর থানা-পুলিশ আছে কেন, মামলা কেন হল, পুলিশ কেন তদন্ত করছে, আদালত-বিচারক কেন?
এই যে হাজার-লাখ ফেসবুক ব্যবহারকারীর একইসুরে খণ্ডিত মানদণ্ডে মতামত দেওয়া, তাতে কি ঘটনার নির্মোহ তদন্তে প্রভাব পড়ে না ? গুজবের আঁচ কি আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যদের গায়ে লাগে না ? যদি নির্মোহ তদন্তে প্রভাব পড়ে এবং একজন নিরপরাধ মানুষকেও আদালতের কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হয় অথবা ফেসবুকে অতি আলোচনায় ঘটনার মূল রহস্য উদঘাটন কঠিন হয়ে পড়ে, তাহলে দায়টা কাদের উপর বর্তায় ?
এই যে খণ্ডিত মানদণ্ডে নির্ধারিত মতামত দেওয়া, এতে সমাজের অনেক শিক্ষিত- বিবেকবান মানুষও যেমন পিছিয়ে নেই, দু:খের সঙ্গে বলতে হচ্ছে অনেকসময় আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় যারা নিয়োজিত, তাদের অনেকেও এসব বিতর্কে যোগ দেন। চিকিৎসকের আত্মহত্যার ঘটনায় দেখলাম- একদল পুরুষ নারীদের একহাত নিচ্ছেন। আর একদল নারী পুরুষের বিরুদ্ধে লেগেছেন। অথচ আমরা ফেসবুক ব্যবহারকারীদের তো এটা মানবিকতার দৃষ্টিতে বিচার করার কথা ছিল ! আমি কি শুধুই ফেসবুক ব্যবহারকারী, মানুষ নই?
সুতরাং সঠিক বিচার-বিশ্লেষণের অভাব, খণ্ডিত মানদণ্ডে মতামত দেওয়ার প্রবণতা ক্রমশ: সমাজকে খণ্ডে-খন্ডে বিভক্ত করছে। বাড়াচ্ছে সামাজিক অস্থিরতা। সমাজে বিভ্রান্তি তৈরি করছে। রাষ্ট্রের সংস্থাগুলোকে প্রশ্নের মুখে ফেলছে।
কিছু ক্ষেত্রে এই যে বিতর্ক কিংবা বলার স্বাধীনতা, এর থেকে অনেক ভালো কিছুও বের হয়ে আসছে কিংবা আসার সম্ভাবনা তৈরি হচ্ছে। একথা অস্বীকার করার উপায় নেই। কিন্তু সুচিন্তার পরিধি যদি বিস্তৃত করা যায়, তাহলে সেই সম্ভাবনা আরও বেশি জেগে উঠবে, নিশ্চিতভাবে বলতে পারি।
বোস্টন বিশ্ববিদ্যালয়ের এক গবেষণা বলছে- সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমকে যতই সামাজিক বলা হোক না কেন, এটা আসলে ব্যক্তিকে বিচ্ছিন্ন করে দিচ্ছে।
ক্ষুদ্রজ্ঞানে বলি, সমাজ থেকে শুধু নয়, মানুষকে সুচিন্তার জগত থেকেও অনেকক্ষেত্রে বিচ্ছিন্ন করে দিচ্ছে। কারণ, ফেসবুকে আমরা সবসময় নিজের মতের সমর্থনটাই খুঁজি। ‘সহমত ভাই’ বললে আনন্দ পাই। বিরুদ্ধ মত এলে হয়তো হামলে পড়ছি, নয়তো এড়িয়ে যাচ্ছি।
এ এক অদ্ভূত জগত তৈরি হয়ে গেছে! এখন গণমাধ্যম কর্মীদের একটি প্রতিবেদন কিংবা লেখা ভালো কি খারাপ, সেটি নির্ধারণ করে ফেসবুকে সেটি কয়বার শেয়ার হয়েছে, কতটা লাইক পড়েছে তার উপর। অর্থাৎ মানবজীবনের অনেক কিছুরই নির্ণয়ের ভার মানুষ তুলে দিয়েছে ফেসবুকের কাছে। সমষ্টির মতামত নিয়ে ফেসবুক রায় দিচ্ছে, সেটা সবাই গ্রহণ করছে।
আমাদের মধ্যে এই বোধোদয় কখন আসবে যে- ফেসবুক রায় দেওয়ার জায়গা নয়। দেশে আইন-আদালত আছে। আমাদের মধ্যে কখন এই বোধোদয় আসবে- যে ঘটনা সাদা চোখে দেখি তার মধ্যে অর্ধসত্যও আছে। ফেসবুকে যা লেখা হয় তা অনেকক্ষেত্রেই ঘটনার খণ্ডিত অংশ মাত্র।
একটি অপরাধ কিংবা ঘটনা ঘটলে প্রাথমিক তদন্ত হবে, মামলা হবে, নিবিড় তদন্ত হবে, আসামি চূড়ান্ত করা হবে, তদন্তের ফলাফল পুঙ্খানুপুঙ্খ লিখে আদালতে অভিযোগপত্র দেওয়া হবে। বিচারক সাক্ষ্যপ্রমাণ নিবিড়ভাবে বিশ্লেষণ করে, যুক্তিতর্ক শুনে, পর্যালোচনা করে রায় দেবেন। তখনই বলা যাবে, কে দোষী আর কে নির্দোষ ? ফেসবুকে ‘হোয়াট ইজ অন ইউর মাইন্ড’ অপশনে গিয়ে ‘রায় লিখে দেওয়া’ আমার-আমাদের কাজ নয়। আমি বিতর্কে শুদ্ধ হতে চাই, কুতর্কে নয়।
রমেন দাশ গুপ্ত, গণমাধ্যম কর্মী
চট্টগ্রাম, বাংলাদেশ।
-
নিবন্ধ // মতামত
-
27-02-2019
-
-