আজি প্রণমি তোমারে-অমল কৃষ্ণ রায়
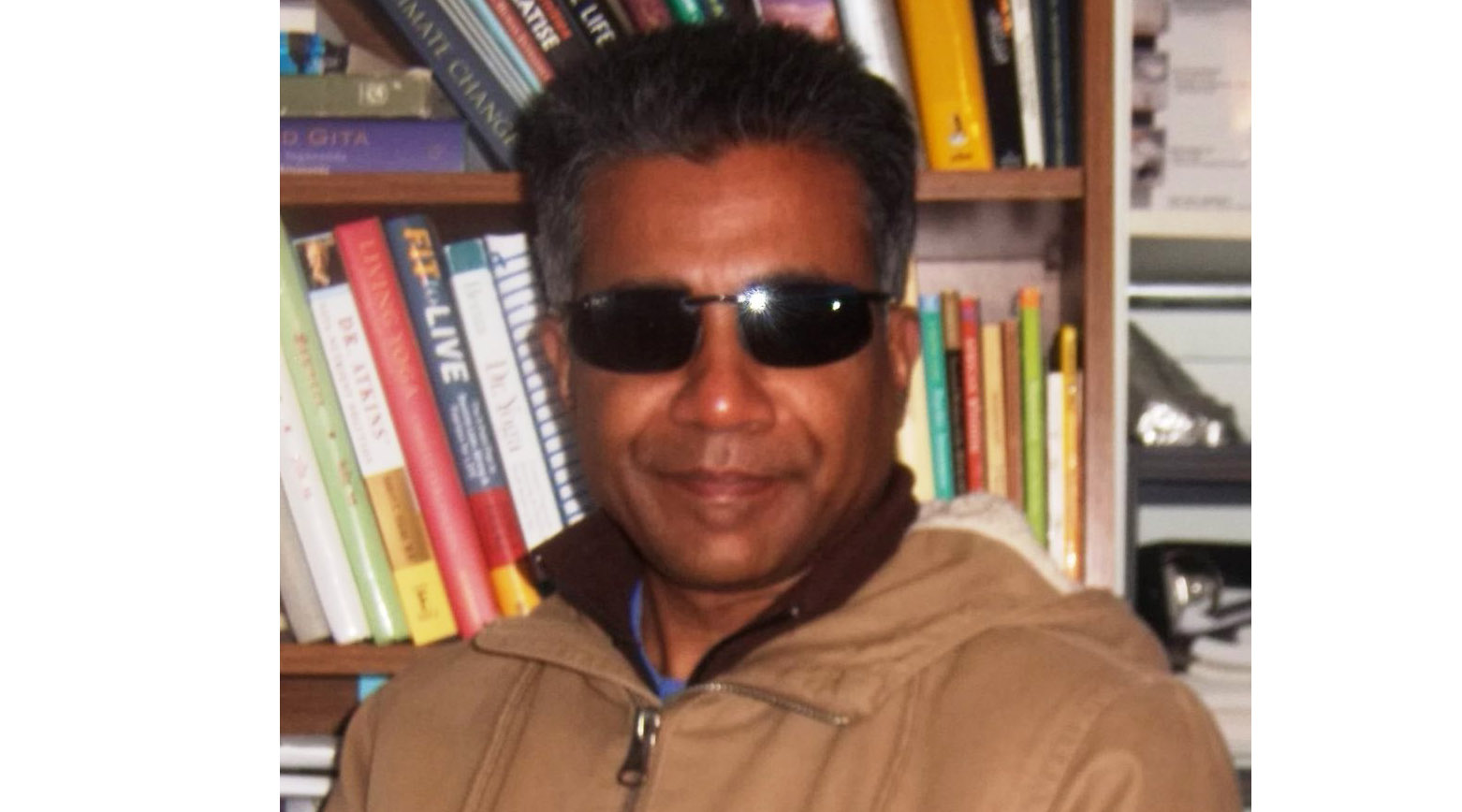
আজি প্রণমি তোমারে
অমল কৃষ্ণ রায়
পঁচিশে বৈশাখ, ১৪২৪ বঙ্গাব্দ। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের একশত-ছাপান্নতম জন্ম-জয়ন্তী। রবীন্দ্রনাথ ছিলেন প্রেম ও সৌন্দর্যের কবি এবং এক মহান মানবতাবাদী ও অধ্যাত্ববাদী দার্শনিক। তাঁর মৃত্যুর ছিয়াত্তর বছর পরেও স্থান আর কালের সীমা ছাড়িয়ে আজও তিনি বাঙালী তথা বিশ্বের সকল মুক্তমনা ও সংস্কৃতিবান মানুষের জীবনে প্রাসঙ্গিক। তাঁর এই প্রাসঙ্গিকতার যোগসূত্র তাঁর সুদূর প্রসারী চিন্তা-চেতনা সমৃদ্ধ কালজয়ী সৃষ্টিকর্মে। তিনি তাঁর মানবীয় উচ্চ ভাবনা-চেতনা আর মানুষের চিরায়ত অনুভূতি ভাষার সৌকর্য সাধন আর নিপুন শৈল্পিক উপস্থাপনার মাধ্যমে কাব্য-সঙ্গীত-প্রবন্ধ-গল্পে আর চিত্রকলায় রূপায়িত করে মানুষের চেতনাকে শানিত করেছেন। সাহিত্য সৃষ্টির মাধ্যমে মানুষকে সংস্কৃতিবান হতে মানব ইতিহাসে যে সকল মনীষী বিশেষ অবদান রেখেছেন রবীন্দ্রনাথ নিঃসন্দেহে তাদের মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ।
আদিম অনগ্রসর মানুষ থেকে আধুনিক সংস্কৃতিবান মানুষের বিবর্তনে অনেক উপাদানের ভূমিকার মত ভাষার ভূমিকা অনস্বীকার্য। বিভিন্ন ভাষার ক্রমবিকাশের ধারায় বাংলা ভাষার বিকাশ আর উৎকর্ষ সাধনে রবীন্দ্রনাথের বিশাল ভূমিকার বিস্তারিত বর্ণনা এখানে বাহুল্য মাত্র। মানব মনের সার্বজনীন ভাব, মানুষের চিরায়ত ধর্ম, মানব কল্যাণ, সৌন্দর্য, প্রেম ও প্রকৃতি প্রীতির উপাদানে সাহিত্য সৃষ্টির মাধ্যমে রবীন্দ্রনাথ বাংলা ভাষা ও সাহিত্যকে বিশ্বসাহিত্যের দরবারে স্থান করে দিয়েছেন।
প্রতিনিয়ত কত আবেগ আর অনুভূতি মানুষের হৃদয়-মনে আলোড়িত হয়! কত সহজ কথা, আবেগ,অনুভূতি,তত্বকথা ভাষায় ব্যক্ত করার নিমিত্তে মানুষের চিরন্তন ব্যকুলতা। কিন্তু প্রায়শই অতি সাধারণ কথাও সহজভাবে ব্যক্ত করা যায় না - মন বেদনাহত হয় সঠিক শব্দটির চয়নের অভাবে আর উপযোগী বাক্যটির রচনার ব্যাঘাতে। রবীন্দ্রনাথের নিজের ভাষায়, "সহজ কথা যায় না বলা সহজে"। কিন্তু আশ্চর্যজনক ভাবে এই অসহজ কাজটি অতি সহজভাবে সম্পাদন করে গেছেন আমাদের রবীন্দ্রনাথ। রবীন্দ্রনাথ অনাবিল সহজতায় সাধারণ মানুষের মনের ভাব, ভালবাসা আর সহজ - সরল - সার্বজনীন অনুভূতির কথা প্রকাশ করে গেছেন তাঁর সাহিত্য সৃষ্টির মাধ্যমে। আর তাইতো রবীন্দ্র-রচনা একবার পাঠ করলে বারংবার পাঠ করতে ইচ্ছে করে। রবীন্দ্র-সাহিত্য আর দর্শনের সাথে যার একবার পরিচয় ঘটে সে বার বার তাঁর কাছে ফিরে যেতে চায়, তার আনন্দ-বেদনায়, সুখে- দুঃখে রবীন্দ্রনাথে আশ্রয় খুঁজে পায়।
রবীন্দ্রনাথ ছিলেন সুন্দরের পূজারী। সৌন্দর্য অবলোকনে, অনুধাবনে আর সৃজনে তিনি ছিলেন সিদ্ধহস্ত। সৌন্দর্য অবলোকনে তাঁর দৃষ্টি ছিল সুদূর বিস্তৃত - এই মর্ত্যলোকের এক বিন্দু শিশির কনা থেকে অন্তহীন মহাবিশ্বের নিঃসীম নীলিমায় এর পরিব্যাপ্তি। তাঁর অপরিসীম সৌন্দর্য চেতনার জোয়ারে তাঁর জীবন থেকে ভেসে গেছে এই মর জগতের সকল অসুন্দর আর ক্ষুদ্রতার গ্লানি। তাই রবীন্দ্রনাথ যখনই কোন অসুন্দরের সন্মুখীন হয়েছেন হয়ত ক্ষনিকের জন্য থমকে দাঁড়িয়েছেন - কিন্তু তাঁর পথ আগলে রাখতে পারেনি - তিনি নিয়ত ধাবমান ছিলেন সুন্দরের আর সত্যের আহবানে । কেবল সৌন্দর্য অবলোকনে আর অনুধাবনেই নয়, সৌন্দর্য সৃষ্টিতেও তিনি ছিলেন অনন্য সাধারণ। রবীন্দ্রনাথ তাঁর অনন্য সাধারণ সৌন্দর্য চেতনায় তাড়িত হয়ে সৃষ্টি করেছেন তাঁর অসাধারণ সৌন্দর্যময়তায় ভরপুর কাব্য আর সঙ্গীত জগৎ। তাঁর সঙ্গীত আর কাব্য সাহিত্য মূলত সত্য আর সুন্দরের জয়গান - এক কথায় তাকে বলা চলে "সৌন্দর্যের নির্যাস"। তাঁর কাব্য জগতে অবগাহন পাঠককে সৌন্দর্যের অপার আনন্দের জগতে ভাসিয়ে নিয়ে চলে, তাঁর সঙ্গীতের নিবিষ্ট অনুরণন শ্রোতাকে মোহাবিষ্ট করে এক অপার্থিব আনন্দানুভূতিতে। সৌন্দর্য সৃষ্টির এই হোলি খেলায় রবীন্দ্রনাথ তাঁর কাব্য আর সঙ্গীত জগতকে উদ্ভাসিত, তরঙ্গায়িত করেছেন নানা ছন্দে আর মাত্রায়। এই সৌন্দর্য সৃষ্টিতে রবীন্দ্রনাথ কখনো আশ্রয় নিয়েছেন পার্থিব দৈহিক সৌন্দর্যের, কখনো প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের আবার কখনোবা চেতনার আলোকে উদ্ভাসিত হয়ে অপার্থিব আনন্দলোকের।
এই সৌন্দর্যের পূজারী রবীন্দ্রনাথ সৌন্দর্যের স্বরূপ বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন,"সৌন্দর্য জাত মানিয়া চলে না, সে সকলের সঙ্গেই মিশিয়া আছে। সে আমাদের ক্ষণকালের মাঝখানেই চিরন্তনকে, আমাদের সামান্যের মুখশ্রীতেই চিরবিস্ময়কে উজ্জ্বল করিয়া দেখাইয়া দেয়। সমস্ত জগতের যেটি মূলসুর সৌন্দর্য সেটি আমাদের মনের মধ্যে ধরাইয়া দেয়, সমস্ত সত্যকে তাহার সাহায্যে নিবিড় করিয়া দেখিতে পাই।"
অপর এক জায়গায় রবীন্দ্রনাথ এই বিশ্বব্যাপী পরিব্যাপ্ত সৌন্দর্য সন্বন্ধে লিখেছেন, " .... .... অতএব আমরা দেখতে পাচ্ছি, জগতের সত্যলোকে আমরা বদ্ধ, সৌন্দর্যলোকে আমরা স্বাধীন। সত্যকে যুক্তির দ্বারা অখন্ডনীয়রূপে প্রমান করতে পারি, সৌন্দর্যকে আমাদের স্বাধীন আনন্দ ছাড়া আর কিছুর দ্বারাই প্রমান করবার জো নেই।"
অপর এক জায়গায় রবীন্দ্রনাথ এই বিশ্বব্যাপী পরিব্যাপ্ত সৌন্দর্য সন্বন্ধে লিখেছেন, " .... .... অতএব আমরা দেখতে পাচ্ছি, জগতের সত্যলোকে আমরা বদ্ধ, সৌন্দর্যলোকে আমরা স্বাধীন। সত্যকে যুক্তির দ্বারা অখন্ডনীয়রূপে প্রমান করতে পারি, সৌন্দর্যকে আমাদের স্বাধীন আনন্দ ছাড়া আর কিছুর দ্বারাই প্রমান করবার জো নেই।"
সুন্দরের প্রতি রবীন্দ্রনাথের এই আকুলতা তাঁর সমস্ত সৃষ্টিকর্মে পরিব্যাপ্ত – তাঁর অনেক গানেই আমরা দেখি বিভিন্ন ধারায় তাঁর এই অসাধারণ সৌন্দর্য চেতনার বর্ণনা। রবীন্দ্রনাথের বৈশিষ্ট্য তিনি সাধারণের মধ্যে অসাধারনত্ব খুঁজে পেতেন। যেমন তাঁর একটি গানে দেখি তিনি তাঁর অসাধারণ সৌন্দর্য চেতনার আলোকে একটি অতি সাধারণ মেয়ের সৌন্দর্যকে ফুটিয়ে তুলেছেন এক অসাধারণ ব্যঞ্জনায়:
"কালো? তা সে যতই কালো হোক
দেখেছি তার কালো হরিণ-চোখ।
.... ...... ...... ...... .......
কৃষ্ণ কলি আমি তারেই বলি
আর যা বলে বলুক অন্য লোক।"
রবীন্দ্রনাথের এই সৌন্দর্য চেতনা তাঁকে সদা ধাবিত করেছে আনন্দলোকে। তাঁর সকল সৃষ্টি কর্মে এই আনন্দের বিস্তৃতি। তাঁর অসংখ্য গানে এই আনন্দের স্বরূপ বিশেষ ভাবে ফুটে উঠেছে:
"আনন্দধারা বহিছে ভুবনে,
দিনরজনী কত অমৃতরস উথলি যায় অনন্ত গগনে।"
--------------------------
"জগতে আনন্দ যজ্ঞে আমার নিমন্ত্রণ।
ধন্য হলো ধন্য হলো মানবজীবন।"
আবার আরেকটি গানে তাঁর অসাধারণ বর্ণনা:
"বহে নিরন্তর অনন্ত আনন্দধারা।
বাজে অসীম নভোমাঝে অনাদি রব
,জাগে অগণ্য রবিচন্দ্রতারা"
রবীন্দ্রনাথ এই নিরন্তর আনন্দধারায় অবগাহন করে সকলকে আনন্দময় হতে আহবান করেছেন অত্যন্ত সহজ সরল অথচ এক গভীর ব্যঞ্জনাময় ভাষায়:
"সদা থাকো আনন্দে, সংসারে নির্ভয়ে নির্মল প্রাণে।
জাগো প্রাতে আনন্দে,করো কর্ম আনন্দে,
সন্ধ্যায় গৃহে চল হে আনন্দগানে।"
রবীন্দ্রনাথ প্রেমের কবি। তাঁর এই প্রেম মানুষ ও প্রকৃতিকে কেন্দ্র করে উৎসারিত হয়ে মর্ত্যলোক ছাড়িয়ে অমৃতলোক পরিব্যাপ্ত। এই প্রেম লৌকিক থেকে অলৌকিকে উত্তরিত। প্রেমের জয়গান রবীন্দ্রনাথের সমস্ত সৃষ্টি জুড়ে। এই প্রেম মানুষকে এই মর জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত করে অমৃতলোকে ধাবিত করে - এই প্রেমের বর্ণনা দিতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন -"প্রেম কে ? তিনিই প্রেম যিনি কোনো প্রয়োজন নেই তবু আমাদের জন্য সমস্তই ত্যাগ করেছেন। তিনিই প্রেম স্বরূপ। তিনি নিজের শক্তিকে বিশ্বব্রহ্মান্ডের ভিতর দিয়ে নিয়ত আমাদের জন্য উৎসর্জন করছেন - সমস্ত সৃষ্টি তাঁর কৃত উৎসর্গ। আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে। আনন্দ থেকেই এই যা-কিছু সমস্ত সৃষ্টি হচ্ছে, দায়ে পড়ে কিছুই হচ্ছেনা - সেই স্বয়ম্ভূ সেই স্বত -উৎসারিত প্রেমই সমস্ত সৃষ্টির মূল।" এই স্বয়ম্ভূ প্রেমের আলোকে রবীন্দ্রনাথের জীবন উদ্ভাসিত - তাঁর সমস্ত সৃষ্টি কর্মে এর জ্যোতি:
"এই- যে তোমার প্রেম, ওগো হৃদয়হরণ,
এই- যে পাতায় আলো নাচে সোনার বরণ "
রবীন্দ্রনাথের প্রেম আর পূজা পর্যায়ের গান বিশ্বমানবের সম্পদ। তাঁর "গীতাঞ্জলি" কাব্যগ্রন্হ এক পরমসত্ত্বার উদ্দেশে প্রেমাঞ্জলি। রবীন্দ্রনাথ এই পরমসত্ত্বার প্রেমের মহিমায় আলোকিত - তাঁর প্রেম পর্যায়ের গানে সেই প্রেমালোকেরই প্রতিচ্ছায়া:
"জানি জানি তোমার প্রেমে সকল প্রেমের বাণী মেশে,
আমি সেইখানেতেই মুক্তি খুঁজি দিনের শেষে।"
রবীন্দ্রনাথ তাঁর এই অসীম, অনন্ত প্রেমের আলোকে এক সর্বভূতে বিরাজমান পরমসত্ত্বা ঈশ্বরের অস্তিত্ব অনুভব করেছেন - তাঁর নিজের কথায়: "ঈশ্বর যে আছেন এবং সর্বত্রই আছেন এ কথাটা যে আমার জানার অভাব আছে তা নয়, কিন্তু আমি অহরহ সম্পূর্ণ এমন ভাবেই চলি, যেন তিনি কোনোখানেই নেই। এর কারণ কী ? তাঁর প্রতি আমার প্রেম জন্মে নি, সুতরাং তিনি থাকলেই বা কী আর না থাকলেই বা কী! তাঁর চেয়ে আমার নিজের ঘরের অতি তুচ্ছ বস্তুও আমার কাছে বেশি করে আছে। প্রেম নেই বলেই তাঁর দিকে আমাদের সমস্ত চোখ চায় না, আমাদের সমস্ত কান যায় না, আমাদের সমস্ত মন খোলে না। এই জন্যেই যিনি সকলের চেয়ে আছেন তাঁকেই সকলের চেয়ে পাই নে - তাই এমন একটা অভাব জীবনে থেকে যায় যা আর কিছুতেই কোনোমতেই পোরাতে পারে না। ঈশ্বর থেকেও থাকেন না - এত বড়ো প্রকান্ড না- থাকা আমাদের পক্ষে আর কী আছে!"
রবীন্দ্রনাথ সমস্ত বিশ্বজুড়ে সবকিছুর মধ্যেই এই পরম সত্ত্বার অস্তিত্ব অনুভব করেছেন। তাঁর অনেক গানের বাণীতেও এই সত্য গভীর ব্যঞ্জনায় মূর্ত হয়ে উঠেছে:
"ভুবনজোড়া আসনখানি
আমার হৃদয় -মাঝে বিছাও আনি।।
...... .......... ........... .........
তোমার আকাশ-ভরা সকল বাণী
-আমার হৃদয়-মাঝে বিছাও আনি।।"
প্রাচীন ভারতীয় ধর্ম-সাহিত্য উপনিষদের নিখিল বিশ্বের সমস্ত মানবের একাত্মতার বাণী, সর্ব প্রাণীর কল্যানের বাণী, মঙ্গলের বাণী রবীন্দ্রনাথের সমস্ত সৃষ্টিতে ধবনিত ও প্রতিধবনিত। তাই রবীন্দ্রনাথকে উপনিষদের ঋষি হিসাবেও আখ্যায়িত করা হয়।
রবীন্দ্রনাথ গেয়ে গেছেন মিলনের জয়গান - সাম্প্রদায়িক বিচ্ছেদ , জাতিগত বিচ্ছেদ, ধর্মীয় বিচ্ছেদ রবীন্দ্রনাথকে সর্বতোভাবে পীড়িত করেছে। তাই সাম্প্রদায়িক সংঘাতের বিরুদ্ধে রবীন্দ্রনাথের লেখনি সোচ্চার হয়েছে, ধর্মীয় বিবাদের কথা বলতে গিয়ে তিনি ধর্মীয় গোড়ামির প্রতি ধিক্কার দিয়েছেন। এই ভারতীয় উপমহাদেশ বিভিন্ন সময়ে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার বিষবাষ্পে আক্রান্ত হয়েছে। সব মিল সত্ত্বেও কেবলমাত্র বাহ্যিক ধর্মীয় অমিলের কারণে এক প্রতিবেশী আর এক বন্ধু প্রতিবেশীর প্রতি চড়াও হয়েছে, এই ধর্মীয় সংঘাতের কাছে অনেক প্রাণের বলি হয়েছে। এই সংঘাত রবীন্দ্রনাথকে বিশেষ ভাবে আন্দোলিত করেছে। তিনি তাঁর লেখা আর ভাষণে ধর্মের এই বীভৎস রূপকে ফুটিয়ে তুলেছেন মানুষের বিবেককে জাগ্রত করার জন্য। তিনি তাঁর "হিন্দু মুসলমান" নামক প্রবন্ধে লিখলেন - "যে দেশে প্রধানত ধর্মের মিলেই মানুষকে মেলায়, অন্য কোনো বাঁধনে তাকে বাঁধতে পারে না, সে দেশ হতভাগ্য| যে-দেশ স্বয়ং ধর্মকে দিয়ে যে-বিভেদ সৃস্টি করে সেইটে সকলের চেয়ে সর্বনেশে বিভেদ| ...মানুষ বলেই মানুষের যে মূল্য সেইটিকেই সহজ প্রীতির সঙ্গে স্বীকার করাই প্রকৃত ধর্মবুদ্ধি| যে দেশে ধর্মই সেই বুদ্ধিকে পীড়িত করে রাষ্ট্রিক স্বার্থবুদ্ধি কি সে-দেশকে বাঁধতে পারে?"
রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'ধর্মমোহ" নামক কবিতায় সেই কালিমাময় ধর্মের ভয়ংকর রূপটি আরো বিশদভাবে ফুটিয়ে তুললেন:
"ধর্মের বেশে মোহ যারে এসে ধরে
অন্ধ সে জন মারে আর শুধু মরে।
নাস্তিক সেও পায় বিধাতার বর,
ধার্মিকতার করে না আড়ম্বর।"
তিনি শুধু লিখেই ক্ষান্ত থাকেননি, তিনি তাঁর ভাষণে এই হেন আত্মহননকারী ধর্মের কড়া সমালোচনা করলেন। একবার সর্ব ধর্ম-সন্মেলনে ধর্মের মূলতত্ব ও ধর্মের মধ্যে সাম্প্রদায়িকতার বিষক্রিয়ার বিচারের বিষয়ে ভাষণ দিতে গিয়ে বলেছিলেন: "যে ধর্ম আমাদের মুক্তি দিতে আসে সেই হয়ে ওঠে মুক্তি ও স্বাধীনতার প্রচন্ড শত্রু| সব বাঁধনের মধ্যে ধর্মনামাঙ্কিত বাঁধন ভাঙ্গাই সব চেয়ে কঠিন| সব গারদের চেয়ে জঘন্যতম সেটা যা অদৃশ্য, যেখানে মানুষের আত্মা মোহজনিত আত্মপ্রবঞ্চনায় বন্দী|"
রবীন্দ্রনাথ গভীরভাবে অনুভব করেছিলেন যে এই মানবতা বিরোধী বাহ্যিক ধর্মের মোহ থেকে মানুষের মুক্তি না আসা পর্য্যন্ত মানুষের প্রকৃত উন্নতি সম্ভব নয়। তাই তিনি বিজ্ঞান চর্চার প্রতি বিশেষ জোর দিয়েছেন। এ সন্বন্ধে তিনি লিখেছেন, "বুদ্ধিকে মোহমুক্ত ও সতর্ক করবার জন্য প্রধান প্রয়োজন বিজ্ঞানচর্চার|" আমরা জানি রবীন্দ্রনাথ "বিশ্বপরিচয়" নামে বিজ্ঞান বিষয়ক একখানি অনুপম গ্রন্হও রচনা করেন।
জাতিগত বিদ্বেষ অবসানের জন্য, পূর্ব -পশ্চিমের মিলনের জন্য তিনি লেখার সাথে সাথে সারা বিশ্বের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে ছুটে গেছেন। অসংখ্য জায়গায় বক্তৃতার মাধ্যমে তিনি তাঁর মানবতাবাদী দর্শনের স্বরূপ ব্যাখ্যা করেছেন। সারা বিশ্বের মানুষের মিলনের প্রতীক হিসাবে শান্তিনিকেতনে প্রতিষ্ঠা করেছেন এক অনন্য প্রতিষ্ঠান "বিশ্বভারতী"। এই "বিশ্বভারতী" সম্বন্ধে তিনি বলেছেন : "শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়কে বিশ্বের সঙ্গে ভারতের যোগের সূত্র করে তুলতে হবে| ঐখানে সার্বজাতিক মনুষ্যচর্চার কেন্দ্র স্হাপন করতে হবে - স্বাজাতিক সংকীর্ণতার যুগ শেষ হয়ে আসছে ...|" আমরা জানি রবীন্দ্রনাথ তাঁর এই বিশ্বভারতীতে সারা বিশ্ব থেকে কত পন্ডিতকে স্বাগত জানিয়েছেন, মানুষের চিত্তবৃত্তির বিকাশ সাধনে কত বিচিত্র জিনিস নিয়ে সেখানে পরীক্ষা -নিরীক্ষা করেছেন।
রবীন্দ্রনাথ ছিলেন এক মহান ঋষি – এক বিশ্ব-দার্শনিক। তাঁর দর্শন চিন্তার মূল উপাদান এই বিশ্বজগত আর বিশ্ব-চেতনা - প্রতিদিনের শব্দময় জগৎ থেকে নৈঃশব্দিক নৈসর্গিক জগৎ। রবীন্দ্রনাথ নিত্যকার যাত্রী আবার সুদূরের পিয়াসী। সব কিছুকে ঘিরে এই জগত-সংসারের ক্ষণ-স্হায়ীত্ব সন্বন্ধে তিনি ছিলেন বিশেষভাবে অনুভূতিপ্রবণ। তাঁর কাব্য-সাহিত্যে এই ভাব বিহ্বলতার সুর বিভিন্ন ভাবে ধ্বনিত ও প্রতিধ্বনিত। তাঁর "শা-জাহান " কবিতায় আমরা পাই তাঁর এই অভিব্যক্তির শৈল্পিক উপস্হাপনা:
"এ কথা জানিতে তুমি ভারত-ঈশ্বর শা-জাহান,
কালস্রোতে ভেসে যায়, জীবন যৌবন ধনমান।"
আবার তাঁর "শেষের কবিতা"য় ফুটে উঠেছে এই সত্য রূপেরই আরো গভীর ব্যঞ্জনা:
"কালের যাত্রার ধ্বনি শুনিতে কি পাও?
তারি রথ নিত্যই উধাও
জাগাইছে অন্তরীক্ষে হৃদয়স্পন্দন
-চক্রে পিষ্ট আঁধারের বক্ষ ফাটা তারার ক্রন্দন।"
কালের করাল গ্রাসে সব কিছুই বিলীন হয়ে যায় এই প্রবল অনুভূতির ধারক হয়েও রবীন্দ্রনাথ ছিলেন অযাচিত ভাবে জীবন-মুখীন| এই অনন্ত বিশ্বের সৃষ্টিতত্ত্বের অমোঘ ধারার প্রতি শ্রদ্ধাবান, এই জগৎ ও জীবনের আসা যাওয়ার চিরন্তন নিয়মের প্রতি আত্মসমর্পিত প্রাণ| আর তাইতো তাঁর গানে সমভাবে ধ্বনিত হয় মৃত্যু আর অমৃতের জয়:
জয় অমৃত তব, জয় মৃত্যু তব,
জয় তিমিরনিবিড় নিশীথিনী ভয়্দায়িনী।
জয় প্রেম মধুময় মিলন তব, জয় অসহ বিচ্ছেদবেদনা।"
রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিগত জীবনে একে একে তাঁর প্রায় সব অতি আপনজনদের চলে যেতে দিতে হয়েছে - কিন্তু ঋষি রবীন্দ্রনাথ, দার্শনিক রবীন্দ্রনাথ পরাজয় বরণ করেননি এই আপাত ভয়্দায়িনী মৃত্যুর কাছে। তাইতো রবীন্দ্রনাথের গানে ফুটে উঠেছে:
“আছে দুঃখ, আছে মৃত্যু, বিরহদহন লাগে।
তবুও শান্তি, তবু আনন্দ, তবু অনন্ত জাগে।"
এই মহান দার্শনিক ঈশ্বর, মানুষ, প্রেম, প্রকৃতি, পূজা,সৌন্দর্য, প্রার্থনা সব কিছু নিয়ে তাঁর নিজস্ব অভিব্যক্তি বর্ণনা করেছেন। সেই বর্ণনায় কোথাও কাউকে আঘাতের চিহ্ন নেই, সেখানে ক্ষুদ্রতা, দীনতা আর বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে, ভূমার সাথে যুক্ত হয়ে মানুষকে সৃষ্টির অনন্ত স্রোতধারায় ভাসাতে চেয়েছেন। তিনি নিজেকে অসীমের সাথে যুক্ত করে, ভূমার সাথে মিলিত হয়ে সব কিছুর উর্ব্ধে উঠে অনন্ত আনন্দধামে সংযুক্ত করেছেন।
রবীন্দ্রনাথ জন্মেছিলেন আজ থেকে একশত একশত-ছাপান্ন বৎসর পূর্বে। আশি বৎসর এই মর্ত্যলোকের আনন্দ যজ্ঞে অবস্হান করে এখন থেকে ছিয়াত্তর বৎসর পূর্বে তিনি এই ইহলোক ত্যাগ করে অমৃতলোকে প্রত্যাবর্তন করেন| কিন্তু তাঁর তিরোধানের সাত দশক পরেও তিনি আজও প্রতিটি মুক্তমনা আর সংস্কৃতিমনা বাঙালীর জীবনে সাড়ম্বরে উপস্থিত। যতই দিন যাচ্ছে ততই রবীন্দ্রনাথের গানের আর কবিতার জনপ্রিয়তা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। আমরা যারা এই ভূপৃষ্ঠের পশ্চিমে বসবাসরত, সঙ্গত কারণেই পূর্বের বিস্তৃত বাঙালী অধ্যুষিত ভূখন্ডের ব্যাপক সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডের অসাধারণ আবহ থেকে আমরা বঞ্চিত| আবার বিভিন্ন কারণে সাহিত্য আর সংস্কৃতি চর্চার সুযোগও এখানে সীমিত, কিন্তু তাই বলে সাহিত্য আর সাংস্কৃতিক চর্চায় প্রবাসী বাঙালীরাও একেবারে পিছিয়ে নেই| প্রবাসে এই সাংস্কৃতিক চর্চায় রবীন্দ্রনাথ আমাদের প্রধান অবলম্বন। রবীন্দ্রচর্চা আমাদেরকে আমাদের শিকড়ের সাথে সম্পৃক্ত করতে সহায়তা করে। আমাদের নতুন প্রজন্মের সন্তানদের আমরা বাঙালী কৃষ্টি আর সংস্কৃতির সাথে পরিচয় করাই রবীন্দ্রচর্চার মাধ্যমে। প্রবাসে অনুষ্ঠিত যেকোনো সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডে, প্রতিটি সংস্কৃতিমনা বাঙালীর গৃহে – রবীন্দ্র-সৃষ্টি-কর্ম ব্যাপক ভাবে উপস্হিত| রবীন্দ্র সঙ্গীতের অনুপস্হিতিতে যেকোনো সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অসম্পূর্ণ এবং প্রায় অকল্পনীয়| এখন এখানে বাঙালী অধ্যুষিত বিভিন্ন শহরে রবীন্দ্র জন্ম জয়ন্তী আর মৃত্যু বার্ষিকী পালিত হয় জাঁকজমক সহকারে| আজ তাঁর এই সার্ধশত জন্ম বার্ষিকীতে আমাদের সবারই প্রার্থনা হোক - যেন এই মহামানবের সর্ব মানবের একাত্মতার বাণী, মিলনের বাণী ও কল্যানের বাণী বিশ্বের প্রতিটি প্রান্তে প্রতিটি মানুষের প্রাণে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হয়, যেন মানুষে মানুষে হিংসা, হানাহানির অবসান হয় - যেন কবিগুরুর সত্য আর সুন্দরের জয়গান প্রতিটি মানুষের জীবনে মূর্ত হয়ে উঠে|
এই বিশ্বকবি ও মহান দার্শনিক এবং সর্বোপরি এই মহামানব আমার জীবন-শিক্ষক, আমার শিক্ষা-গুরু। এই জগৎ, জীবন, মানুষ ও প্রকৃতিকে ভালবাসার এমন শিক্ষা আমি আর কার কাছে পাই? কালিক ব্যবধানের কারণে এই সৌম্য-দর্শন মহাপুরুষকে দর্শন করার আনন্দ থেকে আমার জীবন বঞ্চিত। কিন্তু তাঁর রেখে যাওয়া সৃষ্টিকর্ম - প্রবন্ধ, গল্প, কাব্য, সঙ্গীত আমার নিত্য দিনের অনুষঙ্গ। তাঁর পদ্য ও গদ্য রচনায় জগৎ ও জীবন সন্বন্ধীয় দার্শনিক চেতনা এবং সৌন্দর্য ও প্রেমের বর্ণনা আমাকে ভাবায় - আমার চেতনাকে উর্ধবলোকে ধাবিত করে। তাঁর সৃষ্ট - সঙ্গীতের বাণী, এর অন্তর্নিহিত ভাব আর সুরের ব্যঞ্জনা আমাকে সুখে আরো উদ্বেলিত করে, আমার দুঃখে সান্তনা যোগায় - প্রতিদিনের চেনা জগৎ থেকে আমার অনুভূতিকে এক অচেনা জগতের এক ভিন্ন মাত্রায় উত্তোলিত করে। আজ এই মহামানবের শুভ জন্মবার্ষিকীতে তাঁরই নৈবেদ্যে তাঁর প্রতি নিবেদন করি আমার সশ্রদ্ধ প্রনতি:
“হে মোর চিত্ত, পূণ্য তীর্থে জাগো রে ধীরে
এই ভারতের মহামানবের সাগরতীরে।
হেথায় দাঁড়ায়ে দু বাহু বাড়ায়ে নমি নরদেবতারে
-উদার ছন্দে, পরমানন্দে বন্দন করি তাঁরে।"
ব্যান্ডন, ক্যানাডা
লেখকের অন্যান্য লেখা পড়তে ক্লিক করুন :
ভ্রমণ : হাজার দ্বীপ-এ একদিন - -অমল কৃষ্ণ রায়
-
নিবন্ধ // মতামত
-
20-06-2017
-
-